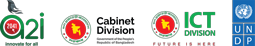-
জেলা সম্পর্কিত
জেলা পরিচিতি
ইতিহাস ও ঐতিহ্য
ভৌগলিক ও অর্থনৈতিক
অন্যান্য
-
জেলা প্রশাসন
জেলা প্রশাসকের কার্যালয়
কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ
শাখা সম্পর্কিত
গুরুত্বপূর্ণ তথ্য
ইনোভাশন কার্যক্রম
-
সরকারি অফিস
আইন-শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা বিষয়ক
স্বাস্থ্য বিষয়ক
প্রকৌশল
কৃষি ও খাদ্য বিষয়ক
-
কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর
-
নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ
-
জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়
-
বীজ বিপণন (বিএডিসি)
-
জেলা মৎস্য অফিস
-
জেলা প্রাণিসম্পদ অফিস
-
মুখ্য পরিদর্শকের কার্যালয়,পাট অধিদপ্তর, নারায়ণগঞ্জ (উত্তর), নারায়ণগঞ্জ
-
পাট অধিদপ্তর
-
বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সি
-
কৃষি বিপণন অধিদপ্তর
-
জেলা বিএডিসি (সেচ) অফিস
-
জেলা ভেটেরিনারি হাসপাতাল, নারায়ণগঞ্জ
-
উদ্ভিদ সংগনিরোধ কেন্দ্র, নদীবন্দর, নারায়নগঞ্জ
-
জেলা কৃত্রিম প্রজনন কেন্দ্র, নারায়ণগঞ্জ
যোগাযোগ ও তথ্য- প্রযুক্তি
শিক্ষা ও সংস্কৃতি
অন্যান্য সরকারি অফিস
-
জেলা-রেজিস্ট্রারের কার্যালয়,নারায়ণগঞ্জ।
-
প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্র
-
নারায়ণগঞ্জ জেলা পরিসংখ্যান কার্যালয়
-
কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর
-
জেলা সঞ্চয় অফিস/বুরো
-
ইসলামিক ফাউন্ডেশন, নারা্য়নগঞ্জ
-
জেলা হিসাব রক্ষণ অফিসারের কার্যালয়, নারায়ণগঞ্জ।
-
জেলা নির্বাচন অফিসারের কার্যালয়, নারায়ণগঞ্জ
-
জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর
-
সামাজিক বন বিভাগ, নারায়ণগঞ্জ
-
একটি বাড়ী একটি খামার প্রকল্প
-
পাসপোর্ট অফিস
মানব সম্পদ উন্নয়ন বিষয়ক
-
কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর
-
স্থানীয় সরকার
জেলা পরিষদ
আড়াইহাজার পৌরসভা
সিটি কর্পোরেশন
উপজেলা পরিষদ
ইউনিয়ন পরিষদ
-
গ্যালারি
ভিডিও গ্যালারি
- অনলাইন শুনানী
-
অন্যান্য প্রতিষ্ঠান
শিক্ষা প্রতিষ্ঠান
সংস্থা/সংগঠন
- ইনোভেশন
-
জেলা সম্পর্কিত
জেলা পরিচিতি
ইতিহাস ও ঐতিহ্য
ভৌগলিক ও অর্থনৈতিক
অন্যান্য
-
জেলা প্রশাসন
জেলা প্রশাসকের কার্যালয়
কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ
শাখা সম্পর্কিত
গুরুত্বপূর্ণ তথ্য
ইনোভাশন কার্যক্রম
-
সরকারি অফিস
আইন-শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা বিষয়ক
স্বাস্থ্য বিষয়ক
প্রকৌশল
কৃষি ও খাদ্য বিষয়ক
- কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর
- নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ
- জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়
- বীজ বিপণন (বিএডিসি)
- জেলা মৎস্য অফিস
- জেলা প্রাণিসম্পদ অফিস
- মুখ্য পরিদর্শকের কার্যালয়,পাট অধিদপ্তর, নারায়ণগঞ্জ (উত্তর), নারায়ণগঞ্জ
- পাট অধিদপ্তর
- বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সি
- কৃষি বিপণন অধিদপ্তর
- জেলা বিএডিসি (সেচ) অফিস
- জেলা ভেটেরিনারি হাসপাতাল, নারায়ণগঞ্জ
- উদ্ভিদ সংগনিরোধ কেন্দ্র, নদীবন্দর, নারায়নগঞ্জ
- জেলা কৃত্রিম প্রজনন কেন্দ্র, নারায়ণগঞ্জ
যোগাযোগ ও তথ্য- প্রযুক্তি
শিক্ষা ও সংস্কৃতি
অন্যান্য সরকারি অফিস
- জেলা-রেজিস্ট্রারের কার্যালয়,নারায়ণগঞ্জ।
- প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্র
- নারায়ণগঞ্জ জেলা পরিসংখ্যান কার্যালয়
- কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর
- জেলা সঞ্চয় অফিস/বুরো
- ইসলামিক ফাউন্ডেশন, নারা্য়নগঞ্জ
- জেলা হিসাব রক্ষণ অফিসারের কার্যালয়, নারায়ণগঞ্জ।
- জেলা নির্বাচন অফিসারের কার্যালয়, নারায়ণগঞ্জ
- জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর
- সামাজিক বন বিভাগ, নারায়ণগঞ্জ
- একটি বাড়ী একটি খামার প্রকল্প
- পাসপোর্ট অফিস
মানব সম্পদ উন্নয়ন বিষয়ক
-
স্থানীয় সরকার
জেলা পরিষদ
আড়াইহাজার পৌরসভা
সিটি কর্পোরেশন
উপজেলা পরিষদ
ইউনিয়ন পরিষদ
-
গ্যালারি
ফটোগ্যালারি
ভিডিও গ্যালারি
-
অনলাইন শুনানী
মামলার তালিকা
এডমিন লগইন
-
অন্যান্য প্রতিষ্ঠান
শিক্ষা প্রতিষ্ঠান
সংস্থা/সংগঠন
-
ইনোভেশন
দাপ্তরিক স্মৃতিকোষ সিস্টেম
ঢাকা বিভাগের মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনা সিস্টেম
মাঠ প্রশাসনের কোভিড ১৯ রিপোর্টিং সিস্টেম
রিপোর্ট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম
পরিত্যক্ত সম্পত্তি ব্যবস্থাপনা সিস্টেম
বার্তা
জেলা ব্র্যান্ডিং- নারায়ণগঞ্জ
বিস্তারিত
জেলা ব্র্যান্ডিং- নারায়ণগঞ্জ
কর্ম-পরিকল্পনা
জেলা প্রশাসন, নারায়ণগঞ্জ
জেলা ব্র্যান্ডিং
নারায়ণগঞ্জের জামদানি
১. ভূমিকা
বর্তমান সরকার ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত করার লক্ষ্যে রূপকল্প-২০২১ এবং ২০৪১ সালের মধ্যে এদেশকে একটি সুখি ও সমৃদ্ধ দেশে রূপান্তরের জন্য রূপকল্প-২০৪১ প্রণয়ন করেছে। উক্ত রূপকল্পসমূহ বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজন দ্রুত এবং ধারাবাহিক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি। এই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনকে ত্বরান্বিত করতে প্রয়োজন সমন্বিত প্রচেষ্টা। বাংলাদেশের প্রতিটি জেলাই বিভিন্নভাবে স্বাতন্ত্র্যমণ্ডিত ও অর্থনৈতিক ভাবে সম্ভাবনাময়। নারায়ণগঞ্জ জেলা তার ব্যতিক্রম নয়। এ-জেলার একটি অত্যন্ত সম্ভাবনাময় পণ্য হলো- জামদানি, যা শিল্পগুণে ও ঐতিহ্যে দেশ-বিদেশে ইতো মধ্যে সুখ্যাতি অর্জন করেছে। যথাযথ পরিকল্পনা ও অবকাঠামোগত সীমাবদ্ধতার কারণে এই শিল্পটির আশানুরূপভাবে বিকাশ লাভ করেনি।
জেলা-ব্র্যান্ডিংয়ের আওতায় জামদানিকে ব্র্যান্ড করা সম্ভব হলে তা এ-শিল্পের বিকাশের মাধ্যমে নারায়ণগঞ্জ তথা দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে সক্ষম হবে।
২. নারায়ণগঞ্জের জামদানির ইতিহাস
জামদানি প্রাচীনকালে তাঁত বুনন প্রক্রিয়ায় কার্পাশ তুলার সুতা দিয়ে মসলিন নামে সূক্ষ্ম বস্ত্র তৈরি হতো এবং মসলিনের উপর যে জ্যামিতিক নকশাদার বা বুটিদার বস্ত্র বোনা হতো তারই নাম জামদানি। জামদানি বলতে সাধারণত শাড়ি বোঝানো হলেও প্রকৃতপক্ষে ঐতিহ্যবাহী নকশায় সমৃদ্ধ ওড়না, কুর্তা, পাগড়ি, ঘাগরা, রুমাল, পর্দা, টেবিল ক্লথ সবই জামদানির আওতায় পড়ে। সপ্তদশ শতাব্দীতে জামদানি নকশার কুর্তা ও শেরওয়ানির ব্যবহার ছিল। মুগল আমলের শেষের দিকে নেপালে ব্যবহৃত আঞ্চলিক পোশাক রাঙ্গা-র জন্য বিশেষ ধরনের জামদানি কাপড় তৈরি হতো।
জামদানির নামকরণ বিষয়ে সঠিক কিছু জানা নেই। তোফায়েল আহমদ (১৯৬৪)-এর মতে ফারসি শব্দ জামা মানে কাপড়, দানা অর্থ বুটি; অর্থাৎ জামদানি অর্থ বুটিদার কাপড়। সম্ভবত মুসলমানরাই জামদানির প্রচলন করেন এবং দীর্ঘদিন তাদের হাতেই এ শিল্প একচেটিয়াভাবে সীমাবদ্ধ থাকে। ফারসি থেকেই জামদানি নামের উৎপত্তি বলে অনুমান করা হয়।
২.১ জামদানির উৎপত্তি ও বিকাশ
বাংলায় বস্ত্রশিল্প এর প্রাচীনতম উল্লেখ পাওয়া যায় কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে (আনু. ৩০০ খ্রি), চর্যাগীতির বিভিন্ন পংক্তি এবং প্লিনির রচনায়, খ্রিস্টীয় প্রথম দশকে রচিত পেরিপ্লাস অব দি এরিথ্রিয়ান সি গ্রন্থে এবং মার্কোপলো, ইবনে বতুতা, চীনা পরিব্রাজক ও ফরাসী রাষ্ট্রদূতের বর্ণনায়। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে বঙ্গ ও পুন্ড্র এলাকায় তৈরি সূক্ষ্ম বস্ত্রের উল্লেখ আছে। বঙ্গ ও পুন্ড্রতে চার প্রকার বস্ত্রের প্রচলন ছিল ক্ষৌম, দুকূল, পত্রোর্ণ ও কার্পাসী।
চিত্র: নকশাদার জামদানি শাড়ি
বিভিন্ন ঐতিহাসিক গ্রন্থ, লোকমুখে প্রচলিত কাহিনী, শ্লোক, বিবরণ থেকে মনে হয় যে, খ্রিস্টপূর্ব প্রথম দশক থেকে বাংলায় সূক্ষ্ম মিহিবস্ত্র সমাদৃত হয়ে আসছিল। বাংলার কার্পাস বা কার্পাস বস্ত্রের বিকাশ ঘটেছে অনেক বিবর্তনের মাধ্যমে। দুকূল নামের বস্ত্রের ক্রমবিবর্তনই মসলিন। জামদানি নকশার প্রচলন ও মসলিনের বিকাশ পাশাপাশি শুরু হয়েছিল মনে হয়। উল্লেখ্য, ইরাকের বিখ্যাত ব্যবসায় কেন্দ্র মসুলে যে সূক্ষ্ম বস্ত্র তৈরি হতো সেটিকে মসুলি বা মসুলিন বলা হতো। নবম শতাব্দীতে আরব ভূগোলবিদ সোলায়মানের স্রিল সিলাত-উত-তওয়ারিখে উল্লেখিত রুমি নামক রাজ্যে সূক্ষ্ম ও মিহি সুতিবস্ত্রের বিবরণ পাওয়া যায়। রুমি রাজ্যকে বাংলাদেশের সঙ্গে অভিন্ন মনে করা হয়। চতুর্দশ শতাব্দীতে ইবনে বতুতা সোনারগাঁয়ের সুতিবস্ত্রের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। ষোড়শ শতাব্দীর শেষ দিকে ইংরেজ পরিব্রাজক র্যালফ ফিচ এবং ঐতিহাসিক আবুল ফজল সোনারগাঁয়ে প্রস্তুতকৃত মসলিনের প্রশংসা করেছেন। জামদানি শিল্পকর্ম পরিপূর্ণতা লাভ করে মোগল আমলে। ঢাকা জেলার প্রত্যেক গ্রামেই কমবেশি তাঁতের কাজ হতো।
১৭৪৭ সালের এক হিসাব অনুযায়ী দিল্লির বাদশাহ, বাংলার নবাব এবং জগৎ শেঠের জন্য সর্বমোট সাড়ে পাঁচ লক্ষ টাকার জামদানি কেনা হয়। একই বছর ইউরোপীয় বণিক ও কোম্পানিরা মোট সাড়ে নয় লক্ষ টাকার মসলিন ক্রয় করে। আঠারো শতকের শেষের দিকে মসলিনের রপ্তানি অনেক কমে যায়। ১৭৬৫ সালে ইংরেজদের দেওয়ানি লাভের পর কোম্পানির নিযুক্ত গোমস্তারা নিজেদের ব্যবসায় উন্নতির জন্য তাঁতিদের ওপর অত্যাচার শুরু করে। তারা নিজেদের ইচ্ছামতো কাপড়ের মূল্য নির্ধারণ করে কাপড় কিনত।
১৭৮৭ সালে James Wise-এর মতে ৫০ লক্ষ টাকা, James Tayler-এর মতে ৩০ লক্ষ টাকার ঢাকাই মসলিন ইংল্যান্ডে রপ্তানি হয়েছিল। ১৮০৭ সালে রপ্তানির পরিমাণ ৮.৫ লক্ষ টাকায় নেমে আসে এবং ১৮১৭ সালে রপ্তানি সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যায়। পরবর্তীকালে ব্যক্তি বিশেষের মাধ্যমে ইউরোপে মসলিন প্রেরণ করা হতো।
উনিশ শতকের মাঝামাঝি জামদানি মসলিনের এক হিসাবে দেখা যায়, সাদা জমিনবিশিষ্ট কাপড়ের উপর ফুল করা ৫০,০০০ টাকার মূল্যমানের জামদানি মসলিন দিল্লি, লখনৌতি, নেপাল, মুর্শিদাবাদ প্রভৃতি এলাকার নবাব-বাদশাহরা ব্যবহার করতেন। এ মসলিন সাধারণত ঢাকার কাটা সুতা দ্বারা তৈরি হতো। উনিশ শতকের মাঝামাঝি জামদানি ও মসলিন শিল্প সংকুচিত হওয়ার পিছনে কতিপয় কারণ কাজ করেছিল। প্রথমত, বিলাতে বস্ত্রশিল্পে মেশিন ব্যবহার, দ্বিতীয়ত, বিলাতি সস্তা সুতা আমদানি এবং তৃতীয়ত, তাঁতিদের প্রতি মুগল বাদশাহ ও তাদের অমাত্যবর্গের অমনোযোগ। ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের পর জামদানি কিছুটা সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা পায়। স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশে ঢাকার অদূরে ডেমরা-য় জামদানি পল্লীর তাঁতিরা কিছুটা আর্থিক সাহায্য পেয়েছেন। তবে মেধা ও শিল্পের সঠিক পারিশ্রমিক না পাওয়ায় অন্যান্য অঞ্চলের তাঁতিরা ইদানীং এ শিল্প টিকিয়ে রাখতে উৎসাহ বোধ করছেন না।
|
|
|
চিত্র: জামদানি প্রস্তুতির কৌশল।
২.২ বুনন পদ্ধতি

সাধারণত সুতা কাটার ওপর নির্ভর করত জামদানি মসলিনের সূক্ষ্মতা। সুতা কাটার উপযুক্ত সময় ভোরবেলা। কেননা তখন বাতাসের আর্দ্রতা বেশি থাকে। সুতা কাটার জন্য তাঁতিদের প্রয়োজন হতো টাকু, বাঁশের ঝুড়ি, শঙ্খ ও পাথরের বাটি। মাড় হিসেবে সাধারণত খই, ভাত বা বার্লি ব্যবহার করা হতো। জামদানি তৈরির আগে তাঁতিরা সুতায় মাড় ও রং করে নিতেন। রং হিসেবে বনজ ফলফুল-লতা-পাতার রং ব্যবহার করা হতো। ভাল জামদানির জন্য ২০০ থেকে ২৫০ নম্বরের সুতা ব্যবহূত হতো। অবশ্য আজকাল তাঁতিরা বাজার থেকে নির্ধারিত কাউন্টের সুতা কিনে জামদানি তৈরি করেন এবং প্রাকৃতিক রঙের পাশাপাশি কৃত্রিম রং ব্যবহার করে থাকেন। জামদানি তৈরির ক্ষেত্রে প্রতি তাঁতে দুজন তাঁতি পাশাপাশি বসে কাজ করেন। দুটি সুচাকৃতি বাঁশের কাঠিতে নকশার সুতা জড়ানো থাকে। প্রয়োজনীয় স্থানে সুচ দুটি দিয়ে পরিমিত টানায় সুতার মধ্যে নির্দিষ্ট স্থানে রঙিন সুতা চালিয়ে দেওয়া হয়। এরপর পাশের সুতার মাকু একজন তাঁতি পাশ থেকে অন্য তাঁতির কাছে দিলে তা সেদিক থেকে বের করে দেওয়া হয়। এভাবে তাঁতে রেখে জামদানি নকশা ফুটিয়ে তোলা হয়। জমিনের সুতার তুলনায় নকশার সুতা মোটা হওয়ায় নকশাসমূহ স্পষ্টভাবে ফুটে ওঠে। জামদানি তৈরির প্রথম দিকে ধূসর জমিনে জাম নকশা করা হতো। পরবর্তীকালে ধূসর রং ছাড়াও অন্য রঙের জমিনে নকশা তোলা হতো। ষাটের দশকে জমিনে লাল সুতার নকশা করা জামদানি অত্যন্ত সমাদৃত হয়। ইংল্যান্ডের ভিক্টোরিয়া অ্যান্ড আলবার্ট মিউজিয়ামে সাদা জমিনে সাদা সুতার কাজের সুন্দর জামদানি রক্ষিত আছে।
২.৩ জামদানির প্রকারভেদ
জামদানি নকশার প্রধান বৈশিষ্ট্য এর জ্যামিতিক অলঙ্করণ। জামদানি নকশা বর্তমানের মত কাগজে এঁকে নেওয়া হতো না। দক্ষ কারিগর স্মৃতি থেকে কাপড়ে নকশা তুলতেন। নকশা অনুযায়ী বিভিন্ন জামদানি বিভিন্ন নামে পরিচিত, যেমন পান্না হাজার, দুবলি জাল, বুটিদার, তেরছা, জালার, ডুরিয়া, চারকোণা, ময়ূর প্যাঁচ, কলমিলতা, পুঁইলতা, কচুপাতা, কাটিহার, কলকা পাড়, আঙুরলতা, সন্দেশ পাড়, প্রজাপতি পাড়, দুর্বা পাড়, শাপলাফুল, বাঘনলি, জুঁইবুটি, শাল পাড়, চন্দ্র পাড়, চন্দ্রহার, হংস, ঝুমকা, কাউয়ার ঠ্যাঙা পাড়, চালতা পাড়, ইঞ্চি পাড় ও বিলাই আড়াকুল নকশা, কচুপাতা পাড়, বাড়গাট পাড়, করলাপাড়, গিলা পাড়, কলসফুল, মুরালি জাল, কচি পাড়, মিহিন পাড়, কাঁকড়া পাড়, শামুকবুটি, প্রজাপতি বুটি, বেলপাতা পাড়, জবাফুল, বাদুড় পাখি পাড় ইত্যাদি। বর্তমানে শাড়ির জমিনে গোলাপফুল, জুঁইফুল, পদ্মফুল, কলারফানা, আদারফানা, সাবুদানা ইত্যাদি নকশা করা হয়। সাম্প্রতিক সময়ে ঐতিহ্যবাহী জামদানি নকশাকে পুনরুজ্জীবিত করার প্রয়াস চলছে। ছোট ছোট বিভিন্ন ফুলের বুটি তোলা জামদানি বুটিদার নামে পরিচিত। জামদানি বস্ত্রে ছোট ছোট ফুলগুলি যদি তেরছাভাবে সারিবদ্ধ থাকে তাকে তেরছা জামদানি বলে। এ নকশা শুধু যে ফুল দিয়েই হবে তা নয়, ময়ূর বা লতাপাতা দিয়েও হতে পারে। ফুল, লতার বুটি জাল বুননের মতো সমস্ত জমিনে থাকলে তাকে জালার নকশা বলা হয়। সারা জমিনে সারিবদ্ধ ফুলকাটা জামদানি ফুলওয়ার নামে পরিচিত। ডুরিয়া জামদানি ডোরাকাটা নকশায় সমৃদ্ধ থাকে। বেলওয়ারি নামে চাকচিক্যপূর্ণ সোনারুপার জরিতে জড়ানো জামদানি মুগল আমলে তৈরি হতো। এ ধরনের জামদানি সাধারণত হেরেমের মহিলাদের জন্য বিশেষভাবে বোনা হতো।
২.৪ জামদানির অতীত ও বর্তমান
ব্যয়বহুল জামদানির উৎপাদন একচেটিয়াভাবে বহুকাল মোগলদের হাতেই ছিল। ঢাকায় সদর মলমল খাস কুটির দারোগা জামদানি তৈরির জন্য তাঁতিদের দাদন দিয়ে জামদানি বুননে নিয়োগ করা হতো। এভাবে উৎপাদিত জামদানির মূল্য অনেক বেশি হতো। রাজন্য শ্রেণীর জন্য উচ্চমূল্যের জামদানি প্রস্ত্তত হতো রাজকীয় কারখানায়। অভিজাত ধনীরাও নিজেদের ব্যবহার্য জামদানি প্রস্ত্ততের জন্য উচ্চমূল্যের কারিগর নিয়োগ করতেন। বিশ্ববাজারেও এসব বহুমূল্য জামদানির ব্যাপক চাহিদা ছিল। এশিয়া ও ইউরোপের রাজন্যবর্গ প্রায়শ ঢাকাই জামদানির জন্য বিভিন্ন বণিক কোম্পানিকে অর্ডার দিতেন। কিন্তু উনিশ শতকের প্রথমদিক থেকে উচ্চমূল্যের জামদানি উৎপাদন ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে থাকে। তখন স্বল্পদামের মিলের কাপড় বিশ্ববাজার দখল করে নেয়।
বহু বাধা অতিক্রম করে জামদানি একবিংশ শতাব্দীতে এসেও তাঁর ঐতিহ্য রক্ষা করে টিকে আছে। বর্তমানে এর প্রধান সমস্যা, তাঁতশিল্পীরা সঠিক পারিশ্রমিক পান না। একটি ভাল জামদানি শাড়ি তৈরি করতে তাদের এক থেকে দুই মাস সময় লেগে যায়। সে তুলনায় তারা মজুরি পান খুব কম।
২.৫ জামদানি কারপল্লী ও জামদানি শিল্পনগরী
জামদানি পণ্য দেশের বিভিন্ন স্থানে নানা সময়ে তৈরির করা হলেও বংশানুক্রমিক শৈল্পিক মনোবৃত্তিসম্পন্ন কারিগর/স্থানীয়ভাবে প্রাপ্ত কাঁচামাল, শীতলক্ষ্যার পানি থেকে উত্থিত বাষ্প সুতা প্রস্ত্ততি ও কাপড় বুনার জন্য সহায়ক বিধায় ঢাকার অদূরে রূপগঞ্জ উপজেলার তারাবো ইউনিয়নের ১৪টি গ্রাম ও সিদ্ধিরগঞ্জ ইউনিয়নের ১টি গ্রাম মোট ১৫টি গ্রামে মূলত জামদানি শিল্প কেন্দ্রীভূত। গ্রামগুলি হলো: নোয়াপাড়া, দক্ষিণ রূপসী, রূপসী কাজীপাড়া, গন্দবপুর, সিদ্ধিরগঞ্জ, মুগুরাকুল, খিদিরপুর, ইমকলী, তারাবো, খালপাড়া, দিঘবরার, খাদুন, পবনকুল ও সুলতানবাগ। তাছাড়া গঙ্গানগর, কাহিনা, মীরগদাই, মাহিমপুর, হরিণা নদীর পাড়, মীরকুটিরছেও ও সোনারগাঁওয়ের কিছু কিছু এলাকায় জামদানি তৈরি হয়। বর্তমানে বোয়ালমারী উপজেলায় উন্নতমানের জামদানি পণ্য উৎপাদিত হচ্ছে।
১৯৮২ সন থেকে জামদানি শিল্পকে আরো উন্নত ও মুনাফামুখী করার জন্য Bangladesh Small Industries Corporation (BSIC) নানামুখী উদ্যোগ গ্রহণ করে। অধিক জামদানি শিল্পসমৃদ্ধ রূপগঞ্জের তারাবো ইউনিয়নে বিসিক ১৯৬২-৬৩ ও ১৯৬৪-৬৫ সালে দু’টি জরিপ চালায়। এই জরিপে যথাক্রমে ১৪৬৬টি ও ১১৭৩টি জামদানি শিল্প ইউনিটের অস্তিত্ব পাওয়া যায়। স্বাধীনতা পরবর্তীকালে বিসিক ১৯৯৩ ও ১৯৯৯ সালে রূপগঞ্জের তারাবো ইউনিয়নের ১৪টি, সিদ্ধিরগঞ্জ ইউনিয়নের ১টি সহ মোট ১৫টি গ্রামে ২টি জরিপ কাজ পরিচালনা করে। উক্ত গ্রামসমূহে ১৯৯৩ সালে তাঁতীর সংখ্যা ছিল ১১১৯ জন ও ১৯৯৯ সালে ৭৫৩ জন। ১৯৯৯ সালে তাঁতের সংখ্যা ছিল ২৮৪৫টি। পরবর্তীকালে ২০০২ সালের জরিপে ইউনিট সংখ্যা ছিল ১৫২৮টি, চালু তাঁতের সংখ্যা ছিল ২৫১৯টি, কর্মরত জনশক্তি ৫,৬৬৯ জন।
জামদানি শিল্প বিকাশের জন্য ১৯৯২ সালে বাংলাদেশ সরকার এ খাতের কারুশিল্পীদেরকে প্রয়োজনীয় সহায়তা দানের নিমিত্তে অবকাঠামোগত সুবিধাদি প্রদান, জামদানি উদ্যোক্তাদের পুনর্বাসন, দক্ষ জনগোষ্ঠির আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন, কারুশিল্পীদের অন্য পেশায় চলে যাওয়া রোধ, নতুন প্রজন্মের কারুশিল্পীদের উৎসাহ প্রদান, বাজার চাহিদা অনুযায়ী নকশা ও নমুনা সরবরাহ করা, লাগসই প্রযুক্তি উদ্ভাবনের মাধ্যমে জামদানি পণ্যের গুণগতমান ও উৎকর্ষতা বৃদ্ধি, উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি ও বিপণনের সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে জামদানি শিল্পনগরী ও গবেষণা কেন্দ্র স্থাপন জন্য বিসিককে দায়িত্ব প্রদান করে। সে প্রেক্ষিতে বিসিক জুলাই ১৯৯৩ থেকে জুন ১৯৯৯ মেয়াদে ৫৮৫.৬৩ লক্ষ টাকা ব্যয়ে নারায়ণগঞ্জ জেলার রূপগঞ্জ উপজেলার তারাবো ইউনিয়নের নোয়াপাড়া গ্রামে জামদানি শিল্পনগরী ও গবেষণা কেন্দ্র স্থাপন করে। জামদানি শিল্পনগরীর বর্তমান অবস্থা (২০১০) মোট জমির পরিমাণ ২০ একর তন্মধ্যে শিল্প প্লটের জন্য জমির পরিমাণ ১৪.৩৯ একর, অফিস ও অন্যান্য কাজে ব্যবহূত জমির পরিমাণ ৫.৬১ একর, মোট প্লট সংখ্যা ৪১২টি (প্রতিটি ১২০০ থেকে ২০০০ বর্গফুট বিশিষ্ট), মোট বরাদ্ধপ্রাপ্ত প্লট ৩৯৯টি, উৎপাদনরত শিল্প ইউনিট ৯০টি, নির্মাণধীন শিল্প ইউনিট ১০৪টি এবং নির্মাণের অপেক্ষায় শিল্প ইউনিট ৬০টি।
৩. জেলা-ব্র্যান্ডিংয়ের উদ্দেশ্য
জামদানির মাধ্যমে নারায়ণগঞ্জ জেলা- ব্র্যান্ডিংয়ের মূল উদ্দেশ্যগুলো হলো:
- জেলার অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে গতি সঞ্চার;
- জেলার অর্থনৈতিক, সামাজিক ও অবকাঠামোগত উন্নয়নের পাশাপাশি নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি;
- জেলার ইতিবাচক ভাবমুর্তি বিনির্মাণ;
- জামদানির পটভূমিতে নারায়ণগঞ্জ জেলার ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির লালন ও বিকাশ;
- স্থানীয় উদ্যোক্তা তৈরি;
- জেলার সর্বস্তরের মানুষকে উন্নয়নের অভিযাত্রায় সম্পৃক্ত করা;
- নারায়ণগঞ্জ জেলার নারী ও প্রতিবন্ধীদের ব্যাপক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি ও নারীর ক্ষমতায়ন;
- দেশ-বিদেশে এই জামদানি পণ্যের বাজার সৃষ্টির প্রসার;
- দারিদ্র্য ও বেকারত্ব দূরীকরণ;
- সামগ্রিকভাবে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখা।
৪. জামদানিকে ব্র্যান্ডিংয়ের বিষয় হিসেবে নির্বাচনের যৌক্তিকতা (জেলাসমূহ তাদের যৌক্তিকতা তুলে ধরবে)
নারায়ণগঞ্জের জামদানি সারাদেশে বহু পূর্ব থেকেই প্রশংসিত ছিল। এ পেশার সাথে নারায়ণগঞ্জের আনুমানিক ২.৫০ লক্ষ মানুষ জড়িত। এ শিল্পের সাথে নারায়ণগঞ্জের প্রায় ৫০ হাজার পরিবার জড়িত। বর্তমানে এ জামদানি দেশে ও দেশের বাইরেও সমাদৃত হচ্ছে। এছাড়া বিশ্বের অনেক দেশে নারায়ণগঞ্জের জামদানি বেসরকারীভাবে রপ্তানি করা হচ্ছে। জামদানির জনপ্রিয়তা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। বর্তমানে নারায়ণগঞ্জ জামদানির জেলা হিসেবে এক নামে পরিচিত।

নারায়ণগঞ্জের সদর ও রূপগঞ্জ উপজেলাতেই জামদানি শিল্পের কম বেশী উৎপাদন হয়। নারায়ণগঞ্জের জামদানির গুণগতমান উন্নত হওয়ায় এবং দাম তুলনামূলকভাবে কম হওয়ায় দেশের বিভিন্ন স্থানে জামদানির বিপুল জনপ্রিয়তা রয়েছে। এ শিল্পের মাধ্যমে বহু বেকার এবং শিক্ষিত লোকের আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে অনেকেই এ সব শিল্পের সাথে জড়িত হয়ে কর্মসংস্থানের পথ খুঁজে পেয়েছে।
নারায়ণগঞ্জের পাট শিল্প ও পোশাক শিল্প নারায়ণগঞ্জকে করেছে মহিমান্বিত। এসব কারণে নারায়ণগঞ্জ জেলার জন্য জামদানিকে ব্র্যান্ডিং এর বিষয় হিসেবে নির্বাচন করা হয়েছে। নিম্নে জামদানিকে ব্র্যান্ড হিসেবে নির্বাচনের যৌক্তিকতা তুলে ধরা হলো:
৫. লোগো ও ট্যাগলাইন

জামদানি, সোনারগাঁ লোক ও কারুশিল্প জাদুঘরের সমন্বয়ে একটি চমৎকার নকশার অংশবিশেষ-কে জেলা-ব্র্যান্ডিংয়ের লোগো হিসেবে নির্বাচন করা হয়েছে।
ট্যাগ-লাইনটি নিম্নরূপ:
“সোনারগাঁ প্রাচীন বাংলার রাজধানী
নারায়ণগঞ্জের সেরা জামদানি”
এ ট্যাগ-লাইনটির মর্মার্থ হলো- এই জামদানির মাধ্যমে শুধু নারায়ণগঞ্জই নয় পুরো বাংলাদেশ পরিচিতি লাভ করবে এবং তা নারায়ণগঞ্জসহ দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখবে।
৬. নারায়ণগঞ্জের জামদানি শিল্পের বর্তমান অবস্থা (ব্র্যান্ডিংয়ের জন্য নির্ধারিত বিষয়ে জেলার বর্তমান অবস্থা তথ্যসহ উল্লেখ করতে হবে-তা না হলে ভবিষ্যৎ অগ্রগতি পরিমাপ করা যাবে না)
জামদানি শিল্পটি এখন যথেষ্ঠ লাভজনক একটি শিল্প। অর্থনৈতিকভাবে অগ্রসর এ জেলায় জামদানি শিল্পটি কমর্সংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে জনগণকে নতুনভাবে বাঁচার প্রেরণা যুগিয়েছে। বর্তমানে এ শিল্পটি গুণগত পণ্য উৎপাদনের মাধ্যমে দেশে ও দেশের বাইরে তার অর্থনৈতিক বাজার সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছে। অর্থাৎ এ-পণ্যটি বর্তমানে ঐতিহ্যগত ও অর্থনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ। নারায়ণগঞ্জ জেলার আনুমানিক ৩ লাখ মানুষ এ-শিল্পের সাথে বর্তমানে জড়িত রয়েছে। প্রায় ১০০০ জন উদ্যোক্তা এ-শিল্পের সাথে জড়িত। এ সকল উদ্যোক্তার অধীনে কয়েক হাজার শ্রমিক কাজ করে। দেশের অন্যান্য জেলায় এ সব পণ্য বিক্রয়ের জন্যে কোন অনুমোদিত বিক্রয় কেন্দ্র নেই। তবে নারায়ণগঞ্জ থেকে পণ্য ক্রয় করে ব্যবসায়ীরা দেশের অনেক স্থানেই এ পণ্যটি বিক্রয় করে থাকেন। নারায়ণগঞ্জ জেলায় জামদানির প্রশিক্ষণ দেয়ার জন্যে জেলায় কোন স্বীকৃত প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট নেই। তবে মহিলা সংস্থা/ যুব উন্নয়ন/ মহিলা সমিতি মাঝে মাঝে প্রশিক্ষণের আয়োজন করে থাকে যা প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল।
৭. কাঙ্ক্ষিত ফলাফল ( ফলাফল এমনভাবে নির্ধারণ করতে হবে যেন তা পরিমাপযোগ্য হয়)
জামদানিকে ব্র্যান্ডিংয়ের মাধ্যমে নিম্নোক্ত ফলাফলসমূহ অর্জনের লক্ষ্যে সার্বিক পরিকল্পনা প্রণয়ন ও কার্যক্রম পরিচালনা করা হবে
- জামদানির বাৎসরিক উৎপাদন: ৪০ % বৃদ্ধি করা
- জামদানির বাৎসরিক বিক্রয়: ৫০ % বৃদ্ধি করা
- কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি: ২৫,০০০ জন
- আর্থিক মূল্যে বিক্রয় বৃদ্ধি: ৩০,০০,০০০ টাকা
- স্থানীয় অর্থনীতিতে অবদান: ৪০%
৮. জামদানি শিল্পের সবল দিক, দুর্বলতা, সুযোগ ও ঝুঁকি বিশ্লেষণ
সার্বিক পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নের সুবিধার্থে প্রাথমিকভাবে নিম্নোক্ত সোয়াট (SWOT) বিশ্লেষণ করা হয়েছে:

সবল দিক
- অনিন্দ্য সুন্দর সুচীকর্ম: সুনিপুণ হাতে কারিগরের মনের মাধুরী মেশানো রঙ দিয়ে নান্দনিক রূপ-রস ও বর্ণ-বৈচিত্র্যে ভরা এই জামদানি।
- ঐতিহ্যর বহিঃপ্রকাশ: জামদানি আমরা প্রতিনিয়ত খুঁজে পাই আমাদের শিল্প, সংস্কৃতি, সমাজ-সভ্যতা, প্রকৃতির অপার সৌন্দর্য, গৌরব গাথা ও সুপ্রাচীন ঐতিহ্য।
- কাঁচামালের সহজলভ্যতা: সাধারণত পুরনো কাপড়ের পাড় থেকে সুতা তুলে অথবা হাট হতে তাঁতিদের কাছ থেকে বাহারি সুতা কিনে সুতা কিনে এনে কাঁথা সেলাই করা হয়। এক সময় পুরনো কাপড় বা শাড়ি ছিল কাঁথা তৈরির প্রধান উপকরণ। বর্তমানে নতুন সুতি কাপড় দিয়ে কাঁথা তৈরি করা হয়। স্থানীয় বাজারেই এই কাঁচামালের সহজলভ্যতা আছে।
- শ্রমিকের সহজ প্রাপ্যতা: অনেকেই এই জামদানিকে প্রধান পেশা হিসেবে বেছে নিয়েছেন। গ্রামের অনেক পরিবারই এই জামদানি তৈরি কে লাভজনক বিবেচনা করে এই ব্যবসা করতে আগ্রহী।
দুর্বলতা
- ন্যায্য মজুরির অভাব: একটি জামদানি বুনতে ৪ জন কর্মীর অন্তত: ০৫ দিন সময় লাগে। তারা মজুরি পান প্রতি জামদানির জন্য ১২০০ থেকে ১৫০০ টাকা। জামদানি বুনতে মোট খরচ পড়ে ৩৫০০ থেকে ৫০০০ টাকা। আদতে জামদানি উৎপাদনে তারা খুব একটা লাভবান হচ্ছেন না। কিন্তু শো-রুমে এই জামদানি অনেক দামে বিক্রি হয়ে থাকে।
- কাঁচামালের গুণগত মান নিয়ন্ত্রণের অভাব: জামদানি তৈরিতে এখনও পুরনো ও কম দামি সুতা দিয়ে তৈরি করা হয়। ফলে জামদানির গুণগত মান নিয়ন্ত্রণের অভাব চোখে পড়ার মতো।
- ডিজাইনে বৈচিত্র্যের অভাব: এখনকার কারিগররা আগের মত বিভিন্ন ধরনের ডিজাইন জানেনা বা বলা যায় যে ডিজাইনটি বেশি বিক্রি হচ্ছে তাই তারা বারবার তৈরি করছে। আর বাণিজ্যিকভাবে জামদানি করা হলে তার শৈল্পিক সৌন্দর্যের দিকে ততটা গুরুত্ব দেয়া হয়না।
- পৃষ্ঠপোষকতার অভাব : জামদানি শিল্পীরা অনেকে শুধুমাত্র দারিদ্র্যতার কারণে জামদানি তৈরি করে। কিন্তু এর যথাযোগ্য মজুরি তারা পায়না। ফলে তারা শিল্পগুণ অথবা নান্দনিক ডিজাইন সম্পর্কে চিন্তা করেনা। যথাযথ পৃষ্ঠপোষকতা পেলে তারা শিল্প মান সম্পন্ন জামদানি তৈরিতে উৎসাহিত হবে।
সম্ভাবনা
- কর্মসংস্থান সৃষ্টি: জামদানি শিল্পের উন্নয়নের সাথে নারায়ণগঞ্জ সহ দেশের অন্যান্য অঞ্চলের কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করা সম্ভব। এর ফলে নারীরাও জামদানি তৈরি ও বিক্রির মাধ্যমে সংসারে অবদান রাখতে পারে। বিভিন্ন ক্ষেত্রে যেমন বাজারজাত করণ, সরবরাহকারী ইত্যাদি ক্ষেত্রে গ্রামের আরও অনেকের জন্য কাজের সুযোগ ও সৃষ্টি করতে পারে। তাহলে গ্রামীণ অর্থনীতিতে দারিদ্র্যতা দূর হবে; সৃষ্টি হবে কর্মসংস্থান।
- বিদেশে রপ্তানির সম্ভাবনা: সারাবিশ্বে এখন জামদানির বিশেষ বাজার তৈরি হয়েছে যার আন্তর্জাতিক খ্যাতি অসামান্য। বিদেশিরা আমাদের এই ঐতিহ্যকে মূল্যায়ন করে এবং লালন করে। বাংলাদেশের জামদানি উন্নত গুণগতমান ও মূল্য তুলনামূলক কম হওয়ায় বর্তমানে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে জামদানির বিশেষ বাজার সৃষ্টি হচ্ছে। ইউরোপ, আমেরিকা ও মধ্যপ্রাচ্যেও জামদানি রপ্তানির বাজার উন্মুক্ত হচ্ছে। এই চাহিদা ও জামদানির যোগানের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে বিদেশে জামদানির বাজার প্রসার করে জামদানিকে আরও গ্রহণযোগ্য করে তোলা হবে।
- দেশে বাজার সৃষ্টি: নারায়ণগঞ্জের জামদানি পণ্যের জন্য দেশের মধ্যে সকল জেলাতে জামদানির বিক্রয় কেন্দ্র থাকলে জামদানির বিপণনে সহায়ক হবে। জামদানি জাতীয় সব ধরনের পণ্য বিক্রয় ও প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা গেলে সারা বছরই জামদানি বিক্রি সম্ভব।
- সম্পূরক শিল্পের বিকাশ: কারিগররা জামদানি তৈরির বর্তমানে ইন্ডিয়ান ও চায়নার সূতা ব্যবহার করে থাকে। একটি জামদানি তৈরিতে ২ থেকে ৪ কেজি সূতা ব্যবহার হয়। এই সুতার ব্যবহারের পরিবর্তে আমাদের দেশীয় সুতার ব্যবহার করা হলে আমাদের দেশের সূতা শিল্পের প্রসার সম্ভব। স্থানীয় তাঁতিরা ও তুলা উৎপাদনকারীরা এতে উপকৃত হবে।
ঝুঁকি
- মধ্যসত্বভোগীদের দৌরাত্ব্য : মধ্যস্বত্বভোগীদের কারণে জামদানি উৎপাদনকারীরা পণ্যের ন্যায্য মজুরি থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। নারায়ণগঞ্জ জেলার জামদানি উৎপাদনকারীদের থেকে এই সুবিধা ভোগীরা অনেক কম দামে জামদানি কিনে নিয়ে শহরে অনেক চড়া দামে তা বিক্রি করছে।
- বাণিজ্যিক হারে একই নকশার ব্যবহার: বর্তমানে জামদানি তৈরিতে পূর্বের কাঁচামাল ব্যবহৃত না হলেও নকশার অনুকরণ ব্যাপকভাবে দেখা যায়। পুরনো দিনে প্রথমে নকশা করে জামদানি না করার কারণে প্রতিটি জামদানির আলাদা আলাদা রূপ ছিল, ভিন্নতা ছিল। অধিকাংশ সময় জামদানির নকশা মোটেও না এঁকে সরাসরি তাঁতে জামদানি তৈরি করেন তারা। কিন্তু বর্তমানে নিজ উদ্যোগে বাজার জাত করার কারণে নকশা নকল করে চাহিদা অনুযায়ী সরবরাহ করা হয়। ফলে জামদানির বিশেষত্বটা ধীরে ধীরে হারিয়ে যাচ্ছে। ঐতিহ্যের সংরক্ষণের কোন উদ্যোগ এখনও গ্রহণ করা হচ্ছেনা।
- সৃজনশীল তার অভাব: এখন আর আগের মত ঘরে ঘরে কাঁথা সেলাই এর তেমন প্রবণতা দেখা যায়না। ফলে এখনকার নারীরা আগের মত বিভিন্ন ধরনের ফোঁড় জানেনা। আর বানিজ্যিকভাবে কাঁথা সেলাই করা হলে তার শৈল্পিক সৌন্দর্যের দিকে ততটা গুরুত্ব দেয়া হয়না।
৯. জেলার ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও মুল্যবোধকে ব্র্যান্ডিং এর সম্পৃক্তকরণ ( এ বিষয়সমূহকে ব্র্যান্ডিং কার্যক্রমের সাথে কীভাবে সম্পৃক্ত করা হবে তা উল্লেখ করতে হবে)।
জামদানি আবহমান বাংলার একটি অন্যতম নিদর্শন। এর মাধ্যমে ক্রমান্বয়ে নারায়ণগঞ্জের বিভিন্ন ঐতিহাসিক ঘটনা, বিভিন্ন সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, উপকথা ইত্যাদিকে ফুটিয়ে তুলার উদ্যোগ ইতোমধ্যে গৃহীত হয়েছে এবং তা অব্যাহত থাকবে।
১০. জেলা-ব্র্যান্ডিংবাস্তবায়নকর্ম-পরিকল্পনা
জেলা ব্র্যান্ডিং বাস্তবায়নের জন্য তিন বছর মেয়াদী নিন্মোক্ত কর্ম-পরিকল্পনা অনুসরণ করা হবে:
- স্বল্পমেয়াদ: ০৬মাস
- মধ্যমেয়াদ: ০১ বছর ০৬মাস
- দীর্ঘমেয়াদ: ৩বছর
কর্ম-পরিকল্পনা ছক
|
নং |
কার্যক্রম |
কর্মসম্পাদন সূচক |
দায়িত্বপ্রাপ্ত কমিটি |
সময়সীমা |
সহায়তাকারী |
|||||||||||
|
১ |
সংশ্লিষ্ট সকলের অংশগ্রহণে মতবিনিময় এবং ব্র্যান্ডিং এর বিষয় নির্দিষ্টকরণ |
মতবিনিময় অনুষ্ঠিত এবং বিষয় নির্ধারিত |
জেলা কমিটি |
ইতোমধ্যে অনুষ্ঠিত এবং বিষয় নির্ধারিত |
জেলার জনগণ |
|||||||||||
|
২ |
একজন জেলা ফোকাল পয়েন্ট নির্ধারণ ও বিভিন্ন কমিটি ও উপকমিটি গঠন এবং দায়িত্ব বিভাজন |
ফোকাল পয়েন্ট ও বিভিন্ন কমিটি গঠিত |
জেলাকমিটি |
এপ্রিল-২০১৭ |
------ |
|||||||||||
|
৩ |
নাম, লোগো ও ট্যাগ-লাইন নির্ধারণ |
চিহ্নিত |
সংশ্লিষ্ট কমিটি |
এপ্রিল-২০১৭ |
জেলার সকল অংশীদার |
|||||||||||
|
৪ |
উদ্দেশ্য ও কাঙ্খিত ফলাফল নির্ধারণ |
উদ্দেশ্য ও কাঙ্খিত ফলাফল নির্ধারিত |
সংশ্লিষ্ট কমিটি |
এপ্রিল ২০১৭
|
জেলার সকল অংশীদার |
|||||||||||
|
৫ |
পণ্যের বর্তমান উদ্যোক্তা,বাজার, অবকাঠামো ও অন্যান্য বিষয় সম্পর্কে প্রাথমিক গবেষণা |
গবেষণা প্রতিবেদন |
সংশ্লিষ্ট কমিটি |
এপ্রিল-২০১8 |
জেলার সকল অংশীদার |
|||||||||||
|
৬ |
জামদানিকে ব্র্যান্ড করার ক্ষেত্রে SWOT বিশ্লেষণ |
প্রতিবেদন |
এপ্রিল-২০১৭ |
এপ্রিল-২০১৭ |
জেলার সকল অংশীদার |
|||||||||||
|
৭ |
সময়াবদ্ধ পরিকল্পনা প্রণয়ন |
পরিকল্পনা প্রণীত |
সংশ্লিষ্ট কমিটি |
এপ্রিল-২০১৭ |
জেলার সকল অংশীদার |
|||||||||||
|
৮ |
জেলার ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও মুল্যবোধকে ব্র্যান্ডিংএর সাথে সম্পৃক্তকরণ |
জামদানিতে প্রতিফলিত |
চলমান |
চলমান |
জেলার সকল অংশীদার |
|||||||||||
|
৯ |
সম্ভাব্য বাজার বিশ্লেষণ |
বিশ্লেষণ প্রতিবেদন |
সংশ্লিষ্ট কমিটি |
জুন-’১8 |
জেলার সকল অংশীদার |
|||||||||||
|
১০ |
প্রচার |
প্রচারের জন্য বিভিন্ন উদ্যোগ গৃহীত |
সংশ্লিষ্ট কমিটি |
চলমান |
মিডিয়াসহ জেলার সকল অংশীদার |
|||||||||||
|
১১ |
ব্র্যান্ডবুক প্রণয়ন |
ব্র্যান্ডবুক প্রণীত |
সংশ্লিষ্ট কমিটি |
মে-২০১8 |
দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যাক্তিবর্গ |
|||||||||||
|
১২ |
পরিকল্পনা বাস্তবায়ন |
দায়িত্ব অনুয়ায়ী কর্ম সম্পাদিত, অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রণীত |
সংশ্লিষ্ট কমিটি |
চলমান |
জেলার সকল স্তরের জনগণ |
|||||||||||
|
১২.১ |
বিভিন্ জেলা ব্র্যান্ডিং এর কর্মপরিকল্পনাব্র্যান্ডিং বিষয়ঃ পণ্য (জামদানী) তিন বছর মেয়াদি কর্ম-পরিকল্পনা
কাঙ্ক্ষিত ফলাফল
কর্মপরিকল্পনা ইতিমধ্যে নারায়ণগঞ্জ জেলা ব্র্যান্ডিংয়ের উদ্যোগ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদে বিভিন্ন কর্ম-পরিকল্পনা নেয়া হয়েছে। পাশাপাশি পণ্য উৎপাদন ও বিপণনের মধ্য দিয়ে জেলার ঐতিহ্য তুলে ধরতে বিভিন্ন মেয়াদী উদ্যোগ নেয়ার বিষয়ে বিস্তারিত পরিকল্পনা নেয়া হয়েছে। জামদানী তৈরির আধুনিক সুবিধাদি নিশ্চিত করার লক্ষ্য বেসরকারি বিনিয়োগকারীদের সাথে সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বে প্রকল্প চালুর উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। উল্লেখযোগ্য পরিকল্পনার মধ্যে আরো রয়েছে-
জেলা ব্র্যান্ডিং ভিডিও গ্যালারী |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস